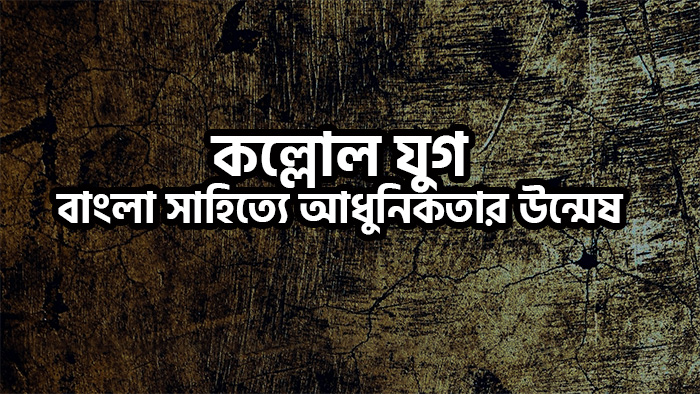কল্লোল যুগ: বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উন্মেষ
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘কল্লোল যুগ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী অধ্যায়। এই সময়কালকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা পর্ব বলা হয়, যখন একদল তরুণ লেখক ও কবি সাহিত্যের চিরাচরিত ধারার বাইরে গিয়ে নতুন ভাবধারার বীজ রোপণ করেন। রবীন্দ্র-আবিষ্ট সাহিত্যের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন বয়স, এক নতুন চেতনার প্রতিফলন ঘটে কল্লোল যুগে। এই নবজাগরণের পটভূমি তৈরি হয়েছিল মূলত ১৯২০-এর দশকের গোড়ার দিকে, যার পরিণত রূপ দেখা যায় ১৯৩০-এর দশকে।
‘কল্লোল’ পত্রিকা: নতুন যুগের সূচক
এই সাহিত্যিক নবযাত্রার মুখপত্র ছিল ‘কল্লোল’ নামের একটি সাহিত্যের সাময়িক পত্রিকা, যার সূচনা হয় ১৯২৩ সালে। দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ ছিলেন এই পত্রিকার মূল কর্ণধার। কল্লোল পত্রিকাটি খুব দ্রুতই সাহিত্যের আঙিনায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর চারপাশে জড়ো হন তরুণ, সাহসী ও চিন্তাশীল কবি-সাহিত্যিকগণ, যাঁরা তখনকার প্রধান ধারার সাহিত্যবিশ্ব—বিশেষত রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আবদ্ধ সাহিত্যের বাইরে এসে নতুন এক বাস্তব, প্রাণময় সাহিত্য নির্মাণে ব্রতী হন।
রবীন্দ্রবিরোধিতা ও আধুনিক বাস্তবতা
কল্লোল যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রবীন্দ্র-প্রভাবের বাইরে গিয়ে সাহিত্যচর্চা। অবশ্যই এ বিরোধিতা কোন বিদ্বেষমূলক ছিল না, বরং রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশালতাকে সম্মান জানিয়েই নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। কল্লোল যুগের সাহিত্যে উঠে আসে সমাজের নিম্নবর্গ, নাগরিক জীবনের টানাপোড়েন, প্রেম-যৌনতা, মানুষ ও সমাজের জটিল বাস্তবতা। এই সময়ের সাহিত্য আরও অনেক বেশি জীবনঘনিষ্ঠ, বাস্তব, বেদনাবিধুর ও আধুনিক।
কল্লোল যুগের পঞ্চপাণ্ডব
এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় বাংলা কবিতার পঞ্চপাণ্ডবের নাম—
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
বুদ্ধদেব বসু
অমিয় চক্রবর্তী
জীবনানন্দ দাশ
বিষ্ণু দে
তাঁরা কেবল আধুনিকতার ধারকই ছিলেন না, বাংলা কবিতার ভাষা, ছন্দ, বিষয়বস্তু ও ভাবনাজগতকে সম্পূর্ণ নতুন এক দিশা দেন।
আরও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক
এছাড়াও কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অবনীনাথ রায় প্রমুখ লেখকদের অবদানও এই যুগে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে কাজী নজরুলের বিদ্রোহী চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ কল্লোল যুগের সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটে নতুন মাত্রা যোগ করে।
অন্যধারার পত্রিকাগুলো
কল্লোল পত্রিকার প্রভাবে ‘প্রগতি, উত্তরা, কালিকলম, পূর্বাশা’ প্রভৃতি সাহিত্যপত্রিকাও গড়ে ওঠে। তবে আধুনিকতার নামে যে কোনো লেখাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে—এই অভিযোগ এনে মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, নীরদ চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে ‘শনিবারের চিঠি’ একটি ভিন্ন বলয়ের পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই দ্বন্দ্বও পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যকে আরও বহুমাত্রিক করেছে।
মূল্যায়ন ও উত্তরাধিকার
কল্লোল যুগ বাংলা সাহিত্যের এক সংঘর্ষ ও সৃষ্টির যুগ। এই সময়ের সাহিত্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মহিমা যেমন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, তেমনি সাহিত্যকে এনে দেওয়া হয় এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি। শুধু কাব্য নয়, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক—সব ক্ষেত্রেই কল্লোল যুগ একটি গঠনমূলক ধাক্কা দেয়।
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত ‘কল্লোল যুগ’ বইটি এই পর্বের ইতিহাস ও বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।
সাহিত্যজগতে নবজাগরণের জন্য প্রয়োজন হয় সময়ের চেতনায় অভ্যুত্থান ঘটাতে পারা একদল দৃষ্টিসম্পন্ন তরুণের। কল্লোল যুগে ঠিক তেমনটাই ঘটেছিল। এই যুগ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। সাহিত্যে প্রগতির পথ তৈরি করেছিল যে ধারা, তা আজও বাংলা সাহিত্যের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। কল্লোল যুগ তাই কেবল একটি সাহিত্যিক আন্দোলন নয়, এক বিপ্লবের নাম।